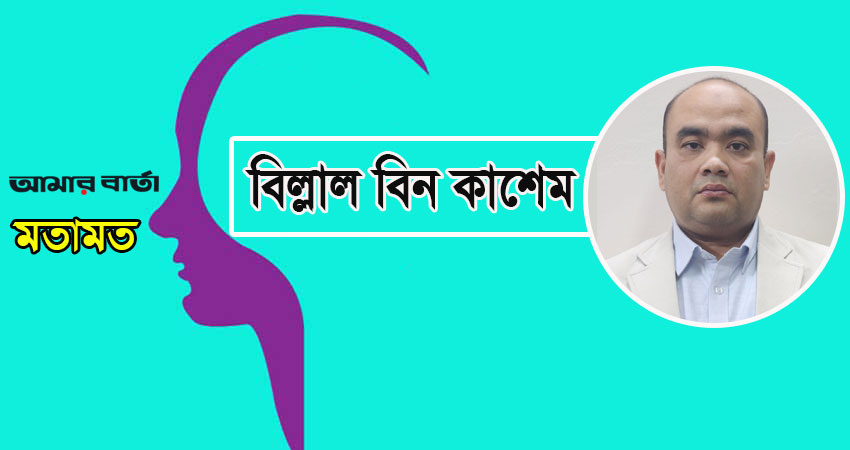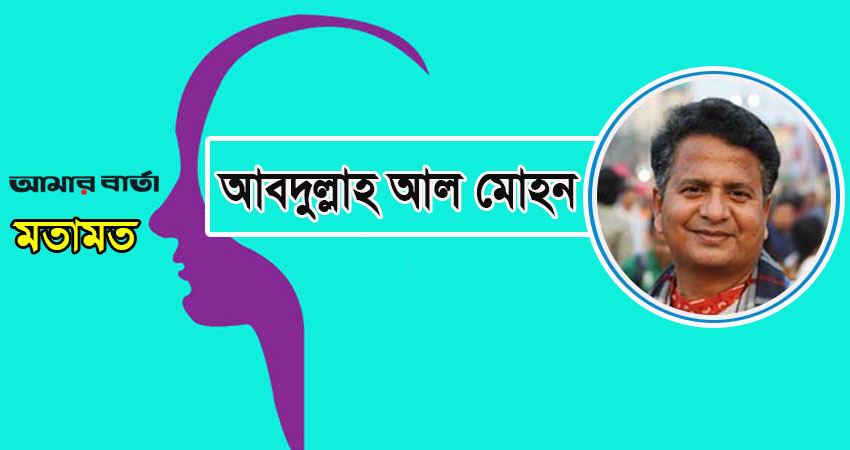
৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। পৃথিবীর অনেক দেশে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এবারের (২০২৫ সালের) জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ‘গ্রন্থাগারে বই পড়ি, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ি’। প্রতি বছরই দিবস যাপনে গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে প্রতিপাদ্য ঘোষণা করা হয়।
‘মহাসমুদ্রের শত বছরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমন্ত শিশুর মতো চুপটি করিয়া থাকিত, তবে সে মহাসমুদ্রের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।’ লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো এত চমৎকার করে বোধহয় আর কেউ বলেননি। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানে তো বটেই, বাঙালি জীবনের জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক চর্চায় গ্রন্থাগারের অনন্য ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই কবিগুরু গ্রন্থাগারকে এতটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, মানব জীবনে গ্রন্থাগারের অবদান সম্পর্কে আমরা সম্ভবত সবচেয়ে কম জানি, জানতে চাইও না। আর সে কারণেই আজকের বাংলাদেশে গ্রন্থাগার এক বিরাট ঐতিহ্যের ধারক হয়েও, একটি ঋদ্ধ উত্তরাধিকারী হয়েও কোনো এক অজানা পরিণতি বহন করতে যাচ্ছে বলে শঙ্কা জাগে। কেননা ক্রমশ পাঠবিমুখ,বইবিমুখ সর্বোপরি জ্ঞানবিমুখ হওয়ার এক উদগ্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে উঠছে বাংলাদেশ, আমরাও। আর এর মূল শিকার হচ্ছে আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোররা এবং অসীম সম্ভাবনাময় যুবসমাজ। তাদের সামনে ‘নষ্ট’ হওয়ার সহজলভ্য কত সহস্র প্রলোভন, বিপরীতে গ্রন্থাগারমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে নানা বাধা আর হতাশার প্রাচীর। অথচ বই ও পাঠকের মেলবন্ধনেই গ্রন্থাগার। আর তাই কমতে থাকা পাঠক নিয়ে আমাদের গ্রন্থাগার বা পাঠাগারগুলো শুধু ভবন আর বই নিয়ে নির্বাসিত কাল যাপন করবে কিনা, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।
আশার কথা হলো, এত কিছুর পরও বাংলাদেশে পাঠাগার গড়ে উঠছে ও পাঠক তৈরি করছে, নিবেদিত কিছু মানুষ আছো স্বপ্ন দেখছে, কাজে নিমগ্ন হয়ে গায়ক কবীর সুমনের বাণীকে ধারণ করে- ‘স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে আমার আজো যে গেলো না’। আর তাই আলোকিত মানুষ গড়তে চাই পাঠাগার, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে গ্রন্থাগার। ২০০৬ সালে মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র কলেজে শুরু হওয়া আমার শিক্ষকতা জীবনে নিরন্তর সংগ্রাম শুরু হওয়া একান্ত স্বপ্নতাড়িত আবেগময় প্রচেষ্টার নাম হয়ে উঠেছে, ‘আলোকিত মানুষ চাই/করি দৃঢ় অঙ্গীকার/গড়ি ঘরে ঘরে পাঠাগার’। যা সময়ের দাবির প্রেক্ষিতে বর্তমানে ‘মানবিক ও যুক্তিবাদী মানুষ চাই/করি দৃঢ় অঙ্গীকার/গড়ি ঘরে ঘরে পাঠাগার’। সেই প্রক্রিয়ারই অংশ হয়ে উঠেছে সৃজনশীল সহশিক্ষার আনন্দময় আয়োজন ‘মঙ্গল আসর’। মূল কাজই হলো সুনির্বাচিত কিছু বই পড়া এবং প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর বাড়িতে সেই সব পঠিত বইয়ের সমাহারে ছোট একটি পারিবারিক গ্রন্থাগার সৃষ্টি ও সমৃদ্ধকরণের। রচনার শুরুতেই এত কথার কারণ ২০১৮ সালে প্রথমবার শুরু হয়ে আমাদের দেশে প্রতি বছর নিয়মিভাবে ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস’ পালিত হচ্ছে, সেই দিবসকে মনে রেখে।
যে অসীম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের প্রতিদিন বাড়িতে বা গ্রন্থাগারে দেখা হয়, তার নাম মুদ্রিত গ্রন্থ, বই। সেই বই, যার উদ্ভব বা আবিষ্কার সভ্যতার ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিলো। সেই বইয়ের মধ্যকার সুপ্ত আলোক শক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমনটি বলেছিলেন, মানবাত্মার অমর আলো থাকে বইয়ের পাতায় পাতায়, সেই বই পড়লেই মানুষের মন বড় হয়। আর আমাদের ‘আলোকিত মানুষ চাই’ আন্দোলনের পুরোধা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার প্রায়ই বলে থাকেন, ‘ছোট মানুষ নিয়ে কখনো বড় জাতি, দেশ তৈরি করা যায় না।’ এক্ষেত্রে জ্ঞানের সূতিকাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থার করুণচিত্র আমাদের প্রবল আশাহত করে, বেদনা জাগায়, গভীরতর অসুখে আক্রান্ত করে। শুরুতেই তাই অপ্রিয় অনুধাবনের কথাগুলো উল্লেখ না করলেই নয়। একজন শিক্ষক হিসেবে এবং ‘মঙ্গল আসর’-এর উদ্যোগে ‘গড়ি ঘরে ঘরে পাঠাগার’ আন্দোলনের একজন ‘নিস্ফলা মাঠের কৃষক’ হিসেবে খুবই বেদনার ও চরম হতাশার সাথে খেয়াল করি, আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা আয়োজনে, অনুষ্ঠানে-প্রতিযোগিতার পুরস্কারে মহামূল্যবান উপহার বই নয়, থালা-ঘটি-বাটি ক্রয় ও প্রদানের মানসিক বিকৃতির অসুস্থ প্রবণতাই বেশি দৃশ্যমান হয়। ফলে আমাদের বইপাঠে প্রেরণাদায়ী শিক্ষকদের গ্রন্থপ্রীতি প্রবল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, বইয়ের প্রতি তাদের চরম স্ববিরোধী মনোভাব ও বাস্তবতাচিত্র মননহীনতার দৈন্যতাকে প্রকট ভাবে তুলে ধরে। আমাদের স্কুল-কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রন্থাগারগুলো আজ বস্তাপঁচা নোটবই আর গাইডে ভরা। প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষদের দুর্নীতি প্রীতিই এর অন্যতম কারণ। শিক্ষাবিরোধী লোভী মনোভাবের ‘চাকুরে’ শিক্ষকদের হাতে পড়ে আমাদের শিক্ষাঙ্গণের গ্রন্থাগারগুলো বেহাল অবস্থায় আছে। বাজেট ব্যয় করা ছাড়া পাঠমুখী সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির দিকে কারো কোন সুনজর নেই ততটা। সরজমিনে যে কেউ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে একবার ঢু মারলে, ক্রয়কৃত, সংগ্রহকৃত বইয়ের দিকে নজর দিলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা, বাস্তবতার প্রমাণ পাবেন, টের পাওয়া যাবে। যিনি বা যারা বইবিরোধী মনোভাবের অধিকারী, যাদের মন অন্ধকারের মৌলবাদে স্থবির, কিন্তু দুর্নীতির বিল-ভাউচারে-ক্রয় কমিটির কাজে দারুণ সুদক্ষ, ঘুরেফিরে সেই তাদের কয়েকজনকেই বই কেনাকাটার সাথে জড়িত থাকতে দেখা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কমিটিগুলোর কয়েক বছরের তালিকা যাচাই করলেও বোঝা যাবে, থলের বেড়ালের রহস্য বেড়িয়ে আসবে নগ্নভাবে। যাদের জীবনের সাথে বইয়ের তেমন কোন সংশ্রবই নেই, তারাই উপদেশ বিতরণ করেন স্রেফ চাকুরির কারণে, জীবনাচরণের বোধ তাড়নায় নয় মোটেই। এভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের মহান উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বিনষ্ট হচ্ছে। পারস্যের কবি শেখ সাদী কথিত বইয়ের গোলাপ বাগানের বদলে স্বার্থপর কতিপয়ের অসততার অপ্রয়োজনীয় ছাপানো কাগজের ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে।
শুধুমাত্র আনন্দ বিতরণই নয়; শুধু শিক্ষা প্রসারেই নয়, মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনার জাগরণে ও ঐক্যের প্রসারে গ্রন্থাগার এক বিশেষ ভূমিকা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সামগ্রিক ধূসর অতীত পেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে আমরা যে উজ্জ্বল উত্তরাধিকারের সন্ধান পাই, সে উত্তরাধিকার কাল, দেশ, মানব সমাজকে দিয়ে খন্ডিত করা যায় না। মানব জ্ঞানের সৃষ্টিগুলোকে উত্তরকালের জন্য সঞ্চয় করেছে মানুষ। সঞ্চয়ের এই বাহ্যিক রূপ এক একটা সোপানের মত। এক একটি সোপানের উপর নির্ভর করে পরবর্তী সোপান নির্মিত হয়েছে। মানুষ একটির পর একটি যোগাযোগ মাধ্যম ও স্থায়ী তথ্য প্রক্রিয়া আবিষ্কার ও সংরক্ষণ করতে চেয়েছে। প্রতিটি মাধ্যম ও প্রক্রিয়া সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অসামান্য দিকচিহ্ন যা গ্রন্থাগারই ধরে রাখে। আর তাই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলিতে গ্রন্থাগার আজকাল একটি অপরিহার্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। জনসংযোগের যে ক’টি উপায় বর্তমানে সুপ্রচলিতত তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার অন্যতম। প্রমথ চৌধুরীর সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করা যায়, “সাহিত্যে চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরী, ... এদেশের লাইব্রেরীর সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল কলেজের চাইতে কিছু বেশি ... আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারেনা।... আমি লাইব্রেরীকে স্কুল-কলেজের উপর স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্চায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজরে মনকে, নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।” আলোকিত মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে জানেন। আর সে জন্য চাই পাঠাগার। এ প্রসঙ্গে মনীষী মুহাম্মদ আব্দুল হাই মন্তব্য করেন, ‘মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার জ্ঞানের সাধনায়, ভাবের আরাধনায় আর নিজেকে উপলব্ধির প্রয়াসে। প্রতি জাতির মানুষই এ সাধনায় নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছে। নিত্য নতুন উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতায় নিজেকে বিচিত্রভাবে বিকশিত করে চলেছে।... পাঠাগার মানুষের জ্ঞানের অক্ষয় ভান্ডার স্বরূপচিত্ত বিকাশের শ্রেষ্ঠ বিহার ক্ষেত্র।’ আর ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখি হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করা সম্রাট রাজাধিরাজরা প্রত্যেকেই তাদের সাম্রাজ্যে গড়ে তুলেছিল বিশাল বিশাল লাইব্রেরি। জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত জনগণ সেখান থেকে আহরণ করত হৃদয়ের খোরাক। বিশ্বের প্রাচীন সব স্থাপনাগুলোর মধ্যে বিভিন্ন যুগের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ লাইব্রেরিগুলো এক অনন্য স্থাপত্য।
গ্রন্থাগারের পড়াশোনা এখন সনাতন ধারা থেকে তথ্য প্রযুক্তির ধারায় শামিল হয়েছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে মানুষের হাতে হাতে যখন স্মার্টফোন কিংবা ট্যাব, তখন একটি পক্ষ বলতে শুরু করেছেন- মানুষ হয়তো এবার কাগজের বই থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু তাতে বইয়ের প্রতি আমার ভালোবাসায় কোনো প্রভাব পড়েনি। আর এ কারণেই আমি লাইব্রেরি পছন্দ করি। আর শিক্ষক হিসেবে মনে করি জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধসম্পন্ন, সৃজনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে ভালো বইয়ের মাধ্যমেই বিবেককে জাগ্রত করা কোন বিকল্প নেই। স্কুল-কলেজে পড়লেই হবে না। শিক্ষার্থীদের সবার আগে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য বেশি বেশি ভালো বই পড়াতে হবে। এমন বই, যা তাদের বিবেক মানবিক ও যুক্তিবাদে চেতনায় জাগ্রত করবে। আর কে না জানে, যে দেশের লাইব্রেরি যত সমৃদ্ধ, সে দেশ তত উন্নত। আর সাধারণ অর্থে লাইব্রেরি বা পাঠাগার সাধারণ মানুষের জ্ঞানার্জনের জন্য এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। লাইব্রেরি বা পাঠাগার, যেখানে থরে থরে সাজানো থাকে বই। নীরব পরিবেশে বই পড়ার জন্যে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর কিছুই হতে পারে না। গ্রন্থাগার হচ্ছে বই, পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, জার্নাল ও অন্যান্য তথ্যের এমন একটি সংগ্রহশালা- যেখানে পাঠকের প্রবেশাধিকার থাকে এবং পাঠক সেখানে পাঠ, গবেষণা কিংবা তথ্যানুসন্ধান করতে পারেন। গ্রন্থাগারের চেয়ে পাঠাগার বা লাইব্রেরি নামগুলোই অবশ্য লোকসমাজে বেশি পরিচিত। উনিশ শতকে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। বিশ শতকের গোড়ায় গ্রামপর্যায়ে গড়ে ওঠে গ্রন্থাগার ক্লাব। তবে এসব ছিল প্রধানত সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ক। মূলত বিশের দশক থেকে গ্রন্থাগার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করে এবং এটি পরিচালনার জন্য প্রবর্তিত হয় গ্রন্থাগার-শাস্ত্র।
মানবসভ্যতার ক্রম অগ্রগতির ধারায় মানুষের অর্জিত জ্ঞান, মহৎ অনুভব সঞ্চিত হয়ে থাকে পাঠাগারে। এর মাধ্যমে পূর্বপুরুষের জ্ঞান সঞ্চারিত হয় উত্তরপুরুষের কাছে। তাই জ্ঞানচর্চা, অন্বেষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। আর শিক্ষার জন্য প্রয়োজন পুস্তক পাঠ ও জ্ঞানার্জন। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও জ্ঞানার্জনের জন্য প্রচুর বই-পুস্তক পড়তে হয়। গ্রন্থপাঠে ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জন করে। মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নে পাঠাগার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি উন্নত। নিয়মিত অধ্যয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা ও উন্নয়নের মাধ্যমেই এসেছে তাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব। পৃথিবীতে যেসব মনীষী অমর হয়ে আছেন, তার মূলে রয়েছে তাঁদের জ্ঞানচর্চা তথা পুস্তক অধ্যয়ন। অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করেই তাঁরা নিজের বিবেক, বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তিকে করেছেন শাণিত। আর সেই জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন সারা বিশ্বকে। আর এই জ্ঞানার্জনের পথে পাথেয় হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। জ্ঞানার্জন তথা পাঠ্যাভ্যাস ব্যতীত কোনো জাতি উন্নত জীবনের অধিকারী হতে পারে না। তাই উন্নত জাতি গঠনে মানসিক ও আত্মিক সাধনা অপরিহার্য। সে ক্ষেত্রে পাঠাগারের ভূমিকা ও অবদান অসামান্য। পাঠাগার তাই জাতীয় বিকাশ ও উন্নতির মানদণ্ড। গ্রন্থাগার ব্যবহার ও বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া জাতীয় চেতনার জাগরণ হয় না। বই পড়ার জন্য বাংলাদেশে এক সময় সরকারি পাঠাগারের পাশাপাশি ছিল বেসরকারি পাঠাগার। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা কোনো সংস্থার সহায়তায় গড়ে ওঠা এসব পাঠাগার পাড়া-মহল্লার পাঠককে করে দিতো নানা ধরনের বই পড়ার সুযোগ। তবে বর্তমানে প্রযুক্তি নির্ভর জীবন এবং পাঠাগারে নতুন বইয়ের সংযোজন না থাকায় পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে পাঠাগারগুলো। গুগল আর উইকিপিডিয়া-তাড়িত সময়ে নতুন প্রজন্মের বই বিমুখতা প্রায় সর্বজনীন।
একটি দেশের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাগারই পারে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে। আমাদের দেশের নীতিনির্ধারক, গবেষক, জ্ঞানীদের কাছে উক্তিটির যথাযথ সত্যতা থাকলেও গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশে তাদের কোনো পদক্ষেপ বা কর্মপ্রচেষ্টা আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা জানি, যে দেশের গ্রন্থাগার যত বেশি সমৃদ্ধ, সেই দেশ তত বেশি উন্নত। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলো সেবা তথা জনবল কাঠামো দেখলে সহজেই ফুটে ওঠে এর করুণ দশা। দেশের গ্রন্থাগারগুলোর মানোন্নয়নে বছরে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য দিনে দুই-একটি সেমিনারে ও সিম্পোজিয়ামে আমাদের নীতিনির্ধারকদের কণ্ঠে গ্রন্থাগার উন্নয়নের বড় বড় নীতিকথা শুনলেও বাস্তবে এসব নীতিকথার কোনোটিই পরে বাস্তবায়ন হয় না। তারা অবশ্যই জানেন একটি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার পারে জাতির ভাগ্য পরির্বতন করতে। কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থিত অধিকাংশ গ্রন্থাগারগুলোর সেবার মান দেখলে সত্যিই অবাগ লাগে। যে গ্রন্থাগার পারে জাতির উন্নয়ন সাধন করতে, সেই গ্রন্থাগারের সার্বিক সেবার মান ও গ্রন্থাগারগুলোকে তথ্যসমৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন করতে সরকার তথা নীতিনির্ধারকদের অনীহা সত্যিই আমার কাছে বোধগম্য নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ সরকারি কলেজ, ইনস্টিটিউটগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাই- অধিকাংশ সরকারি কলেজে লাইব্রেরিয়ানের পোস্ট খালি, সেখানে সহকারী লাইব্রেরিয়ান দিয়ে, আবার কোথাও অফিস সহকারী দিয়ে লাইব্রেরির তদারকির কাজ করানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগ করা হচ্ছে না এবং সেবার মান বাড়ানো হচ্ছে না। যেখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দেশের প্রাণ হচ্ছে লাইব্রেরি। সেই প্রাণকে জাগিয়ে তুলতে প্রতিষ্ঠানের প্রধান তথা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কেন এই অনীহা- এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা ও মাস্টাস কোর্স পরিচালিত হলেও দিন দিন এ বিষয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা শূন্যের কোঠায় পরিণত হচ্ছে। কারণ সরকার তথা নীতিনির্ধারকদের এই বিষয়ের প্রতি ধারণার অভাব এবং গ্রন্থাগার যে দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারে, সে বিষয়ে সচেতনতার অভাবে এ পেশার প্রতি দিন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে।
যদিও এ কথা সত্য, বর্তমানে এতসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলো দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যে সীমিত শক্তি দিয়ে দেশ ও জাতির ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে, যা কিছুটা হলেও মনে আশার সঞ্চয় করে। কেননা গ্রন্থাগার একটি জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক। একটি জাতি প্রকৃতপক্ষে জাতি হিসেবে কত সভ্য কত উন্নত তা তাদের গ্রন্থাগার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই ফুটে ওঠে। উন্নত বিশ্বের জনগণ গ্রন্থাগারের ওপর নির্ভরশীল ও জ্ঞান আহরণে অধিক সচেষ্ট বিধায় তাদের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব হয়েছে। উন্নত দেশগুলো যদি তাদের গ্রন্থাগারগুলোকে সমৃদ্ধি করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে, তবে আমরা কেন পারছি না। যদিও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জনগণের জন্য একমাত্র গ্রন্থাগারই পারে জাতীয় সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে। কিন্তু দেশের গ্রন্থাগারগুলোর সেবার মান ও সেগুলোকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সরকার তথা নীতিনির্ধারকদের গ্রন্থাগার বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাদের অধিক উদাসীনতা ও বৈরিতার কারণে জাতি তার সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন একজন গবেষক বঞ্চিত হচ্ছে তার গবেষণা বিষয় সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য থেকে। কেননা একজন গবেষকের পক্ষে তার গবেষণার কাজ একা পরিচালনার করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই গ্রন্থাগারমুখী হতে হয় ও গ্রন্থাগার উপকরণ মূলত পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন রেফারেন্স সেবা গ্রহণ করতে হয়। বইপত্র ও তথ্য ছাড়া গবেষণা করা আর ঢাল তরবারি ছাড়া যুদ্ধ করা সমান কথা। দেশে বিভিন্ন প্রকার গবেষণার তথ্য সেবামূলক কাজকে ফলপ্রসূ ও তাদের সহযোগিতার জন্য হলেও দেশের গ্রন্থাগারগুলোর সেবার মানোন্নয়ন করাকে জরুরি বলে মনে করি।
একজন গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীর কাছে তাদের জ্ঞান আহরণের প্রকৃষ্ট বাহক হচ্ছে বই। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি বিশ্বের নামকরা বিজ্ঞানীগণ যেমন প্লেটো, এরিস্টটল, রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীরাও গ্রন্থাগারের কাছে ঋণী। যুগে যুগে গ্রন্থাগার নবপ্রজন্মকে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিত্সক, রাজনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের শিক্ষার্থীদের যেখানে ক্লাসের প্রত্যেক বিষয়ের বই কিনে পড়ার মতো আর্থিক অবস্থা নেই, এ কথা জানা সত্ত্বেও এদেশের গ্রন্থাগারগুলোর সেবার মানোন্নয়নে এবং শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারমুখী করতে উচ্চপর্যায়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করাও জরুরি। আশা করি, আজকের শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা ও মনন দিয়ে সঠিক গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবার মাধ্যমে একদিন দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং একটি উন্নত দেশ জাতিকে উপহার দিতে পারবে। অন্তত তাদের কথা চিন্তা করে হলেও দেশে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলো উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া তেমনি প্রয়োজন বলে মনে করি। জাতীয় সংস্কৃতির ধারক-বাহক এসব গ্রন্থাগারকে বাঁচাতে সরকারের নীতিনির্ধারকদের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গ্রন্থাগার। শিক্ষার প্রসার, গবেষণা, দৈনন্দিন জীবনযাপন, সমাজের মানোন্নয়ন, সমাজের মানুষকে প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে, সমাজ থেকে অশিক্ষা দূর করতে তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গ্রন্থাগার যে একটি জাতির প্রাণকেন্দ্র- এই বোধ প্রতিটি জনগণের মাঝে জাগিয়ে তুলতে পারলেই একটি দেশ, সমাজ তথা একটি জাতির সত্যিকারের ভাগ্য উন্নয়ন ও সার্বিক সমৃদ্ধি সম্ভব হবে। তাই সবাইকে গ্রন্থাগার উন্নয়নে একযোগে কাজ করার পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলো অধিক ব্যবহারের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকগণ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করবেন- জাতি এমনটিই প্রত্যাশা করে।
গ্রন্থাগারের ইতিহাসের পানে তাকালে দেখতে পাই, সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সভ্যতার এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় একের পর এক কীর্তিস্তম্ভ গড়ে তুলেছে মানুষ, সমৃদ্ধ হয়েছে নানা অর্জনে। মানুষের চিরন্তন কীর্তির তালিকায় এমনই একটি অসাধারণ অর্জন গ্রন্থাগার। জ্ঞান সৃষ্টি, সেই জ্ঞানের কাঠামোবদ্ধ সংরক্ষণ এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে জ্ঞানের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ নিশ্চিত করেছে গ্রন্থাগার। সভ্যতার সেই আদিকাল থেকেই কোনো না কোনো রূপে লিপিবদ্ধ জ্ঞানকে সংরক্ষণ করে আসছে মানুষ। ইতিহাসের একেবারে প্রাথমিক পর্বে গ্রন্থাগারগুলো আধুনিক গ্রন্থাগারের চেয়ে একেবারেই অন্য রকমের ছিল। গ্রন্থাগার ইতিহাসবিদরা এগুলোকে ‘প্রোটো লাইব্রেরি’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এগুলো ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে গড়ে তোলা সংগ্রহশালা যেগুলো কালের আবর্তে এক সময় গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। গ্রন্থাগার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্দিরে গড়ে ওঠা সংগ্রহশালা গুলোই গুরুত্বের বিচারে এগিয়ে ছিল। মিশর, প্যালেস্টাইন, ব্যাবিলন, গ্রিস এবং রোমে গ্রন্থাগারের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে মন্দির গ্রন্থাগার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এরপরই উল্লেখ করতে হয় সরকারি দলিলদস্তাবেজের সংগ্রহ বা আর্কাইভসের কথা। গ্রন্থাগারের আদিমতম নিদর্শনগুলোর মধ্যে সরকারি নথির সংগ্রহাগার একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এসব দলিলপত্র লিপিবদ্ধ হত পোড়ামাটির ফলক, প্যাপিরাস বা পার্চমেন্ট রোল এবং কখনও তাম্র বা ব্রোঞ্জপাত্রে। তবে যেআকারেই সংরক্ষিত হোক না কেন, সরকারি কর্মকান্ডের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে ইতিহাস রচনার একটি অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে এসব সংগ্রহ। সরকারি দলিল ও মন্দির সংগ্রহের মতই ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের ফলস্বরূপ সৃষ্ট দলিলপত্রও গ্রন্থাগার উদ্ভবের আদি পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মিশর, ফিনিশীয়া, ব্যাবিলন এবং পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয়া, এথেন্স ও রোমের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রগুলোতে এ ধরনের সংগ্রহ প্রচুর দেখা যেত। গ্রন্থাগারের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সংগ্রহও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। লিখিত দলিলপত্রের সবচেয়ে প্রাচীন উদাহরণগুলোর মধ্যে বেশ কিছু দলিল আছে যেগুলো ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে লেখা। ব্যাবিলনের অধিবাসীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর পূর্বাভাস বা পূর্বলক্ষণের বিবরণ পারিবারিক সংগ্রহে যোগ করার প্রবণতা ছিল। ধর্মীয় কাহিনী ও ভাষ্য, পূরাণ ও লোককাহিনী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক নথিপত্র পারিবারিক সংগ্রহে যুক্ত হয়ে এগুলোকে আদর্শ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পরিণত করেছিল। এভাবেই পারিবারিক আর্কাইভসমূহ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের পূর্বসূরী হিসেবে কাজ করেছিল এবং গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার একটি অতিস্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়।
যে অসীম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের প্রতিদিন বাড়িতে বা গ্রন্থাগারে দেখা হয়, তার নাম মুদ্রিত গ্রন্থ, বই। সেই বই, যার উদ্ভব বা আবিষ্কার সভ্যতার ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিলো। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা সব সভ্যতায় গ্রন্থাগার ও জ্ঞানচর্চা হাত ধরাধরি করে চলতে দেখি। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ সালে প্যাপিরাসের ব্যবহার, ১০৫ খ্রিস্টাব্দে চীনের হান সম্রাটের কাছে সভাসদ ৎসাই লুন-এর কাগজ ব্যবহারের প্রস্তাব এবং ৩০০-৪০০ খ্রিস্টাব্দে প্যাপিরাসের পরিবর্তে পার্চমেন্ট ব্যবহার থেকে শুরু করে প্রকাশনা-প্রযুক্তির সাম্প্রতিকতম ধাপগুলো, ছাপা, বাঁধাইয়ের ইতিহাস সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর। একেকটি বইয়ের জন্ম মানে একটি নতুন শিশু বা জীবনের সৃষ্টি। বইয়ের উদ্ভব, বিকাশ এবং আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত নানা প্রযুক্তির ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে একটি চমৎকার, তথ্যবহুল, গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে, নিকোল হাওয়ার্ড-এর লেখা, নাম দ্য বুক: দ্য লাইফ অব অ্যা টেকনোলজি, ২০০৬ সালে প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট থেকে গ্রিনউড প্রেস। আবার, মেসোপটেমিয়া, মিশর, গ্রিস, রোম, এশিয়া মাইনর, ভারত, চীন-সর্বত্রই নৃপতিদের উৎসাহ ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে বিখ্যাত সব গ্রন্থাগার। এসবের মধ্যে আসুরবানিপাল, আলেকজান্দ্রিয়া, পার্গামাম ও নালন্দা গ্রন্থাগার বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থাগারের তালিকায় নাম লিখিয়েছে। প্রাচীন অ্যাসিরিয়ার নিনেভা শহরে অবস্থিত এবং রাজা আসুরবানিপাল প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় গ্রন্থাগারটি প্রাচীন বিশ্বের সর্বপ্রথম বৃহৎ গ্রন্থাগার, যাতে হাজার হাজার কাদামাটির ফলক সংরক্ষিত হয়েছিল সে সময়কার শ্রেষ্ঠ সব রচনাকর্ম।
কালস্রোতে সবকিছু হারিয়ে গেলেও গ্রন্থাগার মানুষের জীবনে এক শাশ্বত আলোক উৎস। মানুষের অগ্রগতিতে পাঠাগার এক আলোকদিশারী। সভ্য মানুষের জ্ঞানপিপাসার চিরন্তন আধার পাঠাগার। পাঠাগার মানুষের আকাক্সক্ষায় একটি আলোকিত রত্নভাণ্ডারের মতো সেখান থেকে একটি একটি করে নিটোল রত্ন তুলে সে নিজেকে সম্পদশালী বলে প্রতিপন্ন করে, নিজেকে আলোকিত করে। তাই আলোকিত মানুষ তৈরিতে চাই পাঠাগার। একজন আলোকিত মানুষের আত্মা হয় প্রসারিত, উন্মোচিত। তিনি বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন, জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত তার আত্মা। রাষ্ট্র, সমাজ, গণতন্ত্র, ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা- সব চেতনায় সমৃদ্ধ তার হৃদয়। তিনি শাশ্বত আলার পথের যাত্রী। তার এই পথের দিকনির্দেশক পাঠাগার। পাঠাগার গড়ে তোলে আলোকিত মানুষ। আর তাই আসুন ঘরে-বাইরে সর্বত্র পাঠাগারের সমৃদ্ধির দিকে আরেকটু সুনজর দেই। সবশেষে তাই বলতে চাই, বিশ্বায়ন ও তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লবের মাতাল সময়েও গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার টিকে থাকবে, এই আনন্দ প্রকাশই সুবিবেচনাপ্রসূত একমাত্র কাজ হতে পারে না। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিবর্তন ও উন্নয়নে আজকের যে চেহারা ও কাঠামোগত রূপান্তর সাধন করেছে, সেটাকে সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আরও এগিয়ে নেওয়াই জরুরি। -- (তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট, বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা)
লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভাসানটেক সরকারী কলেজ, ঢাকা।
আমার বার্তা/আবদুল্লাহ আল মোহন/এমই