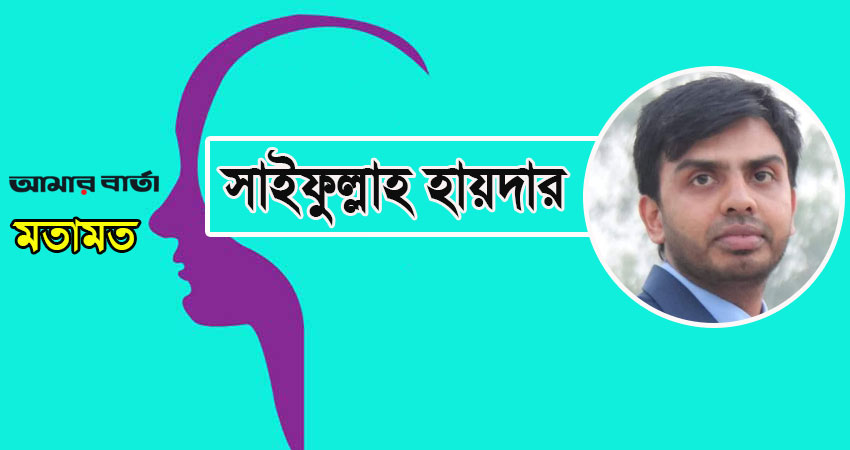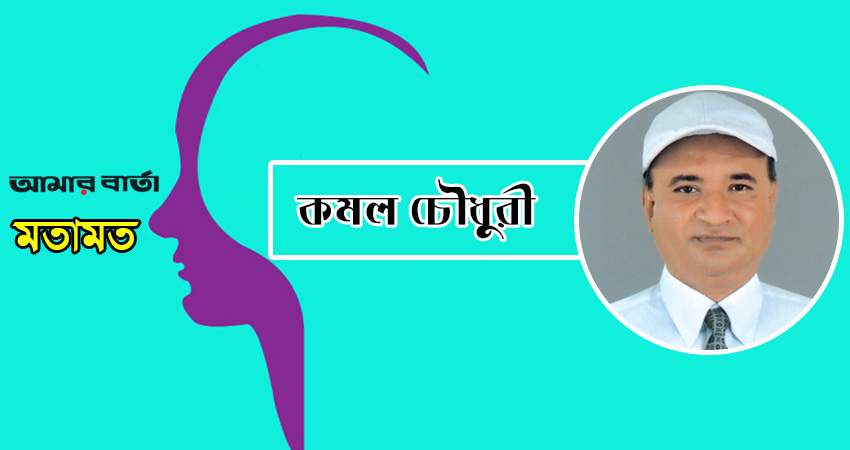ধানের মানুষ ড. আবেদ চৌধুরী একজন স্বনামধন্য, বিশ্ববরেণ্য বাঙালি জিন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানলেখক এবং কবি। দীর্ঘদিন ধরে ধান নিয়ে কাজ করছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার ড.আবেদ চৌধুরী। গবেষণার ফল হিসেবে বোরো জাতের নতুন ধানগাছ উদ্ভাবন করেছেন তিনি। তাঁর উদ্ভাবিত ‘পঞ্চব্রীহি’র একটি ধানগাছ একবার রোপণ করে তা থেকে বছরে পাঁচবার ফলন পাওয়া গেছে। ‘পঞ্চব্রীহি’ ধান,‘রঙিন ভুট্টা’সহ বিভিন্ন নতুন উদ্ভাবন আমাদের নজর কেড়েছে। সাধারণ ভুট্টার সাথে জিনগত পরিবর্তন করে বিভিন্ন রং তৈরি করে এর জেনিটিক্যালি মডিফাইড করে ‘রঙিন ভুট্টা’ উদ্ভাবন করেছেন। ড. আবেদ চৌধুরীর জন্মদিন ১ ফেব্রুয়ারি। ১৯৫৬ সালের এই দিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মদিনে শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় শিক্ষক, গবেষককে, কৃতি এই বাঙালি বিজ্ঞানীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ কম হলেও স্যারের নানা রচনা ও কাজের মাধ্যমেই তিনি আমার পরম শ্রদ্ধার মানুষ হয়ে উঠেছেন। তাঁর জন্মস্থান মৌলভীবাজারের প্রত্যন্ত এলাকা কানিহাটি ঘুরে আসার এবং তাঁর বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের কাজ দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। আমি বিস্ময়ের সাথে তাঁর এবং তাঁর দলের অবিশ্বাস্য আন্তরিকতায় নিরলস সাধনায় গবেষণাকর্মে ব্যাপৃত থাকতে দেখে ভীষণভাবে প্রাণিত হয়েছি। স্যারের সাথে কথা বলেও জিন বিজ্ঞানের অনেক অজানাকে জেনে মুগ্ধ হয়েছি। কৃষি ছাড়াও বিশেষত শিক্ষা বিষয়ে তাঁর ভাবনাগুলো আমাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে বলে নিজেকে স্যারের একজন ছাত্র বলে পরিচয় দিতে ভালো লাগে।
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জিন বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক এবং ক্যানবেরা শহরে বসবাস করেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়াতে আমার ফ্যামিলি রয়েছে, ফ্যামিলির সঙ্গে থাকি। কিন্তু বেশিরভাগ কাজই মরিশাসে, না হয় দেশের ভিতরে এই গ্রামের এখানে করি।’ আবার, তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি করার পর বাংলাদেশে ফিরে আসার বিষয়ে তিনি বলছেন, ‘আমি যেহেতু ফিল্ড চেঞ্জ করেছি। এটি আমাদের দেশে বিরাট একটা সমস্যা। তুমি কেমিস্ট্রি পড়েছ, বায়োলজিতে কেন গেছ, তোমার কেমিস্ট্রিতেও চাকরি হবে না। বায়োলজিতেও চাকরি হবে না। এটা হচ্ছে, আমাদের দেশের নিয়ম। সৌভাগ্যক্রমে দেশে আমাকে চাকরি খুঁজতে হয়নি। বিদেশে হয়ে গেছে। আমি দেশের এই কাণ্ডকারখানা দেখে, আমি চেষ্টাও করিনি। আর আমাদের দেশে ইন্টার ডিসিপ্লিনিয়ারি কাজ কেমিস্ট্রির ব্যবহার বায়োলজিতে। এই রকম কোনো চিন্তা তো আমাদের নেই। এখনও নেই।’
ধানই তাঁর প্রাণ বললে অত্যুক্তি হবে না মোটেই। তাঁর গবেষণা বিষয়ে পাঠ করে আমার আশাবাদ প্রবল হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে তিনি বাঙালির বিজ্ঞান গবেষণার মানকে আরো উচ্চতর অবস্থানে তুলে ধরবেন এবং নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হবেন। আমার এই ইতিবাচক ধারণার স্বপক্ষে অনেক কারণ আছে। ইতিপূর্বে আমরা ফসল বা শষ্য নিয়ে গবেষণায় নোবেল পুরস্কার পেতে দেখেছি। ‘সবুজ বিপ্লব’-এর জনক কৃষি বিজ্ঞানী ড. নরমোন ই বোরলগের নাম মনে আসে। তিনি উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধক গম আবিষ্কারের মাধ্যমে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রভূত অবদানের জন্য ১৯৭০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। জিন বিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী তাঁর ধান গবেষণায় মৌলিক অবদানের জন্যই নোবেল পুরস্কারের দাবিদার হয়ে উঠেছেন বলে আমার বিশ্বাস। কারণ ধানের জিন নিয়ে সফল গবেষণা তাঁকে দিয়েছে বিশ্বজুড়ে সম্মান। তাঁর উদ্ভাবিত নতুন বিভিন্ন জাতের ধানের সফল ফলন হয়েছে।
বিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করলেও দেশমাতৃকার টানে নিয়মিত ছুটে আসেন জন্মভূমিতে। কাজ করছেন পরিবর্তিত জলবায়ু এবং ভূমি উপযোগী ধানের জাত নিয়ে। ধান গবেষণায় নিয়োজিত আছেন ড. আবেদ চৌধুরী। ছিলেন পাটের জিন আবিষ্কারকারী দলে। মরিশাসে ধান চাষে পেয়েছেন সাফল্য। অস্ট্রেলিয়াবাসী জিন বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরীর খেয়াল বিচিত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করলেও পথ বদলে চলে গেছেন বায়োলজিতে। জীববিজ্ঞানই এখন তার ধ্যান জ্ঞান। বিজ্ঞান তার চর্চার বিষয় কিন্তু তার আগ্রহ মূলত সাহিত্যে। পৃথিবীর বহু দেশে তাঁর কাজের চিহ্ন ছড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু নিজের দেশকে ভোলেননি। পারিবারিক জমিতে বিজ্ঞানের খেলা খেলবার মানসে মৌলভীবাজারে ফিরেছেন নিবিড় গবেষণায়। বিচিত্র খেয়ালি এই অন্যরকম বিজ্ঞানীকে সমাজ, রাজনীতি নিত্য ভাবায়। ফলে ‘আলোর মশাল’ নামে সামাজিক প্রতিষ্ঠান খুলে বিচিত্র সব সমাজমনস্ক কাজে জড়িত করেছেন নিজেকে। আর নিজের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা জানতে চাইলে ড. আবেদ চৌধুরী বলেছেন, ‘আমরা বিজ্ঞানকে গ্রামে নিয়ে এসে একটা মডেল চালু করেছি। এই এলাকাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে এখানে একটি ইউনিভার্সিটি হতে পারে। একটা কলেজ অন্তত হতে পারে। কারণ এই যে চিন্তাধারা, এই যে কাজ। এগুলোকে তো ধরে রাখতে হবে। এখন আমরা এইচএসসি মানের যে শিক্ষা, যখন এইচএসসি শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকবে। এটা নিয়ে আমার খুব উৎসাহ। গড়ে তুলেছি একটি নতুন প্রতিষ্ঠান ‘আলোর মশাল’। এই কাজটা হাতে নিয়েছি ‘আলোর মশাল’ এটা শুধু এইচএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, যে কোনো ক্ষেত্রেই শিক্ষাকে একটু আধুনিকীকরণ করা, একটু সাহায্য করা। প্রচলিত ধারার পাশাপাশি। এটাকে কেন্দ্র করে গ্রামে থেকে কিছু হতে পারে। গ্রামে থেকে যেহেতু আমি কাজ করতে ভালোবাসি। এটাই আমি মনে করি, ভবিষ্যৎ।’ ‘আলোর মশাল’ বিষয়ে ড. আবেদ চৌধুরী আরো বলছেন, ‘এলাকার মানুষের সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক। কার ছেলে কে কোথায় পড়ে, আমি সব ছাত্র সম্পর্কে জানি। বিশেষ করে ছাত্র সবাই আমার কাছে আসে। কিন্তু এদের কোনো রোল মডেল নেই। এদের ভালো বলার জন্য, এদের মেধাকে দেখার জন্য কেউ নেই। ‘আলোর মশাল’ হাফেজিয়া খাতুন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যানারে, ওটারই একটা অর্গানাইজড একটা রূপ। এটার একটা সেকশন গ্রামে করে দেব। ছেলেমেয়েদের জন্য।’
বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা। ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে বিএফএফ-সমকাল দ্বিতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অতিথি শিক্ষার্থীদের দেখাতে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলে কয়েকটি ভুট্টা। বক্তৃতার শুরুতে আমাদের দেশে বহুল পরিচিত হলুদ ভুট্টা দেখালেন। তারপর জানালেন, জিন পরিবর্তন করে দিয়ে এই হলুদ ভুট্টা সাদা করা সম্ভব। ব্যাগ থেকে একটি সাদা ভুট্টা বের করে দেখালেন। বললেন, যদি কেউ লাল ভুট্টা খেতে চায় সেটাও সম্ভব; পাশেই রাখলেন লাল রঙের ভুট্টা। এবার সবার চোখ ছানাবড়া। মিলনায়তনের শিক্ষার্থীরা আগ্রহভরে অপেক্ষা করতে লাগল পরবর্তী চমকের জন্য। এবার বের করলেন কালো ভুট্টা। এসবই সম্ভব হয়েছে ভুট্টার জিন পরিবর্তন করে। জানালেন লাল এবং সাদা ভুট্টা পাশাপাশি লাগালে মেন্ডেলের জিনতত্ত্ব অনুযায়ী তাদের জন্ম নিবে বহুবর্ণের ভুট্টা। মিলনায়তনের স্কুল পড়ূয়া তুখোড় বিতার্কিকদের চোখে তখন বিস্ময় ও আনন্দেভরা। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়কে যিনি এত আকর্ষণীয় ও সহজ করে উপস্থাপন করছিলেন তিনি। দেশের কৃষি খাত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে বিজ্ঞানের কারণে কৃষির উৎপাদন বেড়েছে, জমির কারণে নয়। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো, এখানে দেদারসে জমির উপরিভাগ (পলি) ইটভাটায় নেওয়া হচ্ছে, মিল-ফ্যাক্টরি করে ধানি জমি ধ্বংস এবং নগরায়ণ করা হচ্ছে। এর ফলে আগামীতে আমাদের কৃষি বিভাগ হুমকির মুখে পড়বে। কৃষি খাত নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। সেই সঙ্গে ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে।’
ড. আবেদ চৌধুরীর জন্ম মৌলভীবাজার জেলার কানিহাটি গ্রামে। ১৯৭২ সালে মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি, ১৯৭৪ সালে নটরডেম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে ভর্তি হন। অনার্স শেষ করে ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অরেগন ইনস্টিটিউট অব মলিকুলার বায়োলজি বিভাগে পড়তে যান। ১৯৮৩ সালে জিন বিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করেন। ১৯৮৩ সালে টিউলিপ চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের একমাত্র সন্তান সামি চৌধুরী। তিনি মাসে কমপক্ষে একবারের জন্য হলেও দেশে আসেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ‘শৈবাল ও অন্তরীক্ষ’ গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ। আবেদ চৌধুরীর ইংরেজি এবং বাংলা মিলিয়ে ১০টির বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি বই হলো; ‘মানুষের জিন, জিনের মানুষ’,‘অনুভবের নীলনকশা’,‘শৈবাল ও অন্তরীক্ষ (কবিতা সংকলন)’,‘দুর্বাশিশির ও পর্বতমালা’,‘Paradigm Shift (ইংরেজিত লেখা প্রবন্ধগুচ্ছ)’,‘নির্বাচিত কবিতা’,‘স্বপ্ন সত্ত্বা নদী ও অন্যান্য কবিতা, ‘Anguished Rivers and Other Designs’। নিজের লেখালেখির বিষয়ে তিনি বলেছেন, ‘আমি কবিতার বই বের করেছি। বিজ্ঞান নিয়ে লিখেছি। আবার সেই বিজ্ঞান লেখায় ফিরে আসতেছি। আসলে কাজ এতো বেশি। লেখার সময় পাই না। গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ, শিক্ষার উন্নয়নের কাজ (নতুন একটি কাজ হাতে নিয়েছি)। এটার পরে, আর কোনো সময় থাকে না। সবকিছুতেই অনেক সময় লাগে।’ ‘লেখার সময় কখন বের করেন’ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, ‘লেখার জন্য সময় বের করা খুব কঠিন। প্লেনে অনেক সময় আইডিয়াগুলো আসে। সেই আইডিয়াগুলো পরে লিখে ফেলি। অনেকে লেখা চায়, সেজন্য লিখি। ইংরেজিতে অনেক লিখি, ইংরেজিতে লেখা আমার জন্য অনেক সহজ হয়ে গেছে। আর যেহেতু থিসিস পেপারগুলো ইংরেজিতে লিখতে হয়। সেহেতু অভ্যাস হয়ে গেছে, তবে বাংলাতেও লিখি।’
শৈশব থেকে প্রকৃতির সঙ্গে আবেদ চৌধুরীর বন্ধুত্ব। পাহাড় আর সবুজ বৃক্ষরাজি তাঁকে টানতো খুব। সবুজ বৃক্ষরাজির সঙ্গে ভাবনা বিনিময় করতেন প্রতিনিয়ত। পড়াশোনায় ভালো হওয়ায় তার বাবা-মাও কোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি করতেন না। ছেলের কাজকর্মের ব্যাপারে একটা স্বাধীনতা দিয়ে আসতেন। প্রথম শ্রেণি থেকেই পাঠ্যবইয়ে থাকা ছড়া-কবিতাগুলো সানন্দে মুখস্থ করতেন। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় নিজে নিজে ছড়া তৈরি করতে লাগলেন। প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব তার লেখালেখির সত্তাকে সমৃদ্ধ করেছিল। বড় হয়ে নিজের নামের পাশে কবি তকমাটাও জুটে নিয়েছিলেন। ক্লাসের ভালো ছাত্র হওয়ায় নবম শ্রেণিতে ওঠার পর শিক্ষকেরা তাকে বিজ্ঞান গ্রুপে পড়াশোনা করতে উৎসাহ দেন। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে, পরিবার থেকে এমন কোনো চাপ ছিল না। তাই শিক্ষকদের উৎসাহে এবং বিশ্বেও নামজাদা বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বিজ্ঞান গ্রুপে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলে অবধারিতভাবে ব্যবহারিক ক্লাস করতে হয়। রসায়ন ক্লাসে স্যার বলেছিলেন, কিছু কিছু দ্রবণ আছে একটির সঙ্গে অপরটি মিশালে দ্রবণের বর্ণ পুরোপুরি পাল্টে যায়। একদিন ল্যাবরেটরিতে গিয়ে টেস্টটিউব দিয়ে বিভিন্ন দ্রবণ পরীক্ষা করে তার সত্যতা পান। এটি রসায়নের প্রতি তার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। রসায়নের বিক্রিয়া, পর্যায় সারণী তাকে প্রবলভাবে টানতে থাকে।
নটরডেম কলেজের পাঠ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হলে নিজেই পড়ার বিষয় বেছে নেন রসায়ন। স্নাতক শেষ করে চলে আসেন জীববিজ্ঞানে। নিজেই বলছেন, ‘রসায়নে স্নাতক শেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করি। অরেগন স্টেট ইনস্টিটিউট অফ মলিকুলার বায়োলজি আমার আবেদনে সাড়া দেয়। সে প্রতিষ্ঠানে টিচিং অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে স্কলারশিপ দেয়। স্কলারশিপটি বেশ ভালো ছিল। পড়াশোনা, থাকা-খাওয়ার খরচ উঠে যাবে। সে প্রতিষ্ঠানের ইনস্টিটিউট অব মলিকিউলার বায়োলজি বিভাগে ভর্তি হই। বিষয়টি জীববিদ্যা সম্পর্কিত হলেও রসায়ন বিভাগ থেকে আসা শিক্ষার্থীরা পড়তে পারবেন বলে সুযোগ রাখা হয়। আমি এ সুযোগ কাজে লাগাই। এভাবে আমার পড়াশোনার বিষয় পাল্টে যায়।’ শৈশবে উদ্ভিদের প্রতি ভালো লাগাকে এখানে প্রয়োগ করার একটি সুযোগ পান। ১৯৮৩ সালে জিনবিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। গবেষণা চলাকালে রেকডি নামে জেনেটিক রিকম্বিনেশনের একটি নতুন জিন আবিষ্কার করে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ এ জিন আবিষ্কার নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় প্রচুর গবেষণা হয়েছিল। তারা সাফল্যে পৌঁছাতে পারছিলেন না। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট হেলথ, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং ফ্রান্সের ইকোল নরমাল সুপিরিয়রের মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও গবেষণা করেছিলেন।
টানা ১০ বছর যুক্তরাষ্ট্রে থাকায় বেশ বিরক্ত হয়ে পড়েন। দেশভ্রমণ বিরক্তি কাটাতে পারবে বলে মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসেন। দেশ হিসেবে বেছে নেন অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেক দূরে। এ ভ্রমণচিন্তা একসময় তার বসবাসকারী দেশের নামও পাল্টে দেয়। ‘অস্ট্রেলিয়া দূতাবাসে ভিসার জন্য আবেদন করলে তারা আমার প্রোফাইল দেখে বলেন, আপনি আমাদের দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আবেদন করতে পারেন। আমাদের দেশ আপনার মতো গুণী ব্যক্তিকে বসবাস এবং গবেষণা করার সুযোগ করে দিতে পারলে ধন্য হবে। সে সময় অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছিলাম জাহাজে চড়ে, ঘুরেঘুরে। তাহিতির মতো সুন্দর মনোরম দ্বীপ আকর্ষণ করেছিল। সে দেশে বেড়াতে গিয়ে সত্যি মুগ্ধ হয়ে পড়ি। তাই সেখানে আমার স্ত্রীসহ থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। স্থায়ী ভিসার আবেদন করলে তা হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘সিএসআইআরও’-তে সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে যোগ দিই।’
বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে কয়েক ধরনের পাটের জিন আবিষ্কার হয়েছে। এ আবিষ্কারের পেছনে কাজ করা ব্যক্তিদের একজন আবেদ চৌধুরী। ‘পাটের সঙ্গে আমাদের সোনালি ঐতিহ্য জড়িত। ২০০৬ সাল থেকে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের পাটের জিন আবিষ্কারের গুরুত্বের কথা বলে আসছিলাম। পরবর্তীতে আমার সঙ্গে পরিচয় হয় যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করা বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলমের। তিনি এ কাজে বেশ অভিজ্ঞ। তাঁকে নেতা মেনে আমরা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সরকারের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা পাওয়া যায়। আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখে। গুরুত্ব এবং গবেষণা না করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশীয় ঐতিহ্যবাহী ফসলের প্যাটেন্ট হারিয়েছি। সেদিক থেকে আমরা পাটের প্যাটেন্ট নিজেদের কাছে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি।’
তিন শতাধিক ভ্যারাইটি বা জাতের ধান উদ্ভাবন করছেন ড. আবেদ চৌধুরী। এ বিষয়ে জানাচ্ছেন, ‘এ ধানগুলো আসলে ক্রস থেকে এসেছে। এগুলো এমন নয় যে, প্রত্যেকটি বিশাল জমিতে লাগানো হয়েছে। এগুলোর আরও টেস্টিং দরকার। ৩০০টি ভ্যারাইটি এভাবে বলছি, বিভিন্ন আইডিয়া থেকে আমি ক্রস করেছি। কিছু কিছু ভ্যারাইটির খুব ভালো ফলাফল পেয়েছি। সাকসেসফুল হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে। আরেকটি ভ্যারাইটি করেছি, ধান কাটার পর দ্বিতীয় বার ধান হয়। এরকম ভ্যারাইটি আমরা উদ্ভাবন করেছি। এছাড়া, অনেক লম্বা গ্রেন। কিন্তু বাহিরটা হয়ত কালো। আমাদের কালোজিরা, ছোট। কিন্তু বাহিরটা কালো। গ্রেনটা ছোট। আমরা কালোজিরা আর বাসমতি ক্রস করে করেছি। বাসমতির মতো লম্বা, বাহিরটা কালো। এটার ‘কালোমতি’ নাম দেয়া যেতে পারে।’
‘কাসালথ’ নামে হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশি একটি ধান নিয়ে বিশ্বে হইচই পড়ে গেছে। নেচার নামে এক সাময়িকীতে এ ধানটিকে ভারতীয় বুনোধান হিসেবে দাবি করা হলে আবেদ চৌধুরী তার প্রতিবাদ করেন। ম্যানিলায় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ইরি) তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন কাসালথ বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া একটি উন্নত জাতের ধান। আবেদ চৌধুরী বলেন, কাসালথ ধান বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের কৃষকের প্রিয় একটি ধান। আঞ্চলিকভাবে এ ধানের নাম 'খাছালত'। এরই সাথে ড. আবেদ চৌধুরী দেশীয় নতুন উদ্ভাবন হাফিজা-১, জালালিয়া, তানহা ও ডুম- এ চার জাতের ধানের উদ্ভাবন করে বেশি ফলন পেয়েছেন। আমন মওসুমে এ চার জাতের ধান বীজতলা তৈরি থেকে রোপণ করে আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি ফসলি মাঠ থেকে পাকা ধান এই আশ্বিনেই ঘরে তোলা হয়। আমি সরজমিন পরিদর্শনকালে দেখেছি ড. আবেদ চৌধুরী তার গ্রামের বাড়ি হাজীপুর এলাকায় গড়ে তুলেছেন ধান পরীক্ষা মাঠ। এখানে চলছে ধান বীজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এখানে ধানের একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলারও চেষ্টা করছেন। তিনি দেশের হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন জাতের ধান নিয়ে গবেষণা করছেন। তার গবেষণায় কৃষকদের জন্য একই চাষাবাদে দু'বার ফসল উৎপাদন একটি ব্যতিক্রমী মাত্রা যুক্ত হয়েছে। প্রতিটি জাতের ধান পরীক্ষামূলক চাষাবাদ করে তিনি সফল হয়েছেন জানিয়ে বলেছেন, প্রথমে স্থানীয় কৃষকরা এর সুফল ভোগ করবেন। তারপর সারা দেশের কৃষকরা এর সুফল ভোগ করতে পারেন। বাংলাদেশে অগ্রহায়ণে নতুন ফসল ঘরে তুলে নবান্ন করা হয়। আর অগ্রহায়ণের আগে দেশের বেশির ভাগ কৃষকের ঘরে তেমন খাদ্য থাকে না। তার উদ্ভাবিত ধান আগে ঘরে উঠবে খাদ্য সংকট কাটাতে সাহায্য করবে আর আশ্বিনে নবান্ন করতে পারবে দেশের কৃষক সমাজ।
বাংলাদেশ ছাড়াও মরিশাসে ধান উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছেন তিনি। আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ মরিশাস। সেখানকার অধিবাসীরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তারা খাবার হিসেবে ভাত খেয়ে থাকে। কিন্তু সে দেশে ধান চাষ হতো না। ফলে তাদেরকে ধান বা চাল আমদানি করতে হতো বাইরের দেশ থেকে। ২০০৭ সালে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নাবিন রাম গোলাম আবেদ চৌধুরীকে জানান, তাদের দেশে প্রচুর ইক্ষু উৎপাদন হয়। কিন্তু তাদের ধানের চাষাবাদ প্রয়োজন। যদি সেখানে চাষাবাদ করার মতো ধানের প্রজাতি উদ্ভাবন করে দেয়া হয়, তাহলে খুব ভালো হয়। আবেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী সেদেশে চাষাবাদ উপযোগী ধান উদ্ভাবনে মনোযোগী হন। এবং সে দেশের উপযোগী ধান উদ্ভাবনে সক্ষম হন। মরিশাসে ধানের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করা বিষয়ে ড. আবেদ চৌধুরী জানান, ‘বেশ কয়েক বছর আগে, মরিশাসে আমরা ধান উৎপাদনের একটা প্রোগ্রাম নিয়ে গিয়েছিলাম। মরিশাসের সরকার যে জমিগুলোতে সুগার চাষ করা হয়, আমাদের সে ধরনের জমি দিয়েছিল। সেখানে আমরা নানান ধরনের রিসার্চ করেছি। আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন ধানের জাত লাগিয়েছি। ওখানকার জমি এবং আবহাওয়া উপযোগী ধান আমরা রিসার্চের মাধ্যমে তৈরি করেছি। ওই ধান আমরা সুগার চাষ করা হয়, সেই জমিতে লাগিয়েছি। ভালো ফলাফল পেয়েছি। একটি রাইস ‘মাইটি রাইস’ উদ্ভাবন করেছি। ‘মাইটি রাইস’ নামের চালটির সুগার খুব কম। ‘মাইটি রাইস’ খেলে রক্তে সুগার বাড়ে না। মরিশাসে ধানের আরও অনেক রিসার্চ হচ্ছে। ভবিষ্যতে সুগার আরও কীভাবে কমানো যায়, সেই ধরণের ধানের রিসার্চ হচ্ছে।’
সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে বিভিন্ন সময়ে দেশে-বিদেশে শিক্ষাসহ নানা বিষয়েও আলোচনায় অংশ নিয়ে থাকেন বিশিষ্ট জিন বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী। তেমনি নানা আসরে বলা কিছু প্রয়োজনীয় কথামালার দিকে নজর দেওয়া যাক। তিনি কমলগঞ্জের এক আলাপনে বলেছিলেন, ‘ইচ্ছা আর আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে রাখতে পারলে সকল বাধা অতিক্রম করা যায়। দারিদ্রতা কোন বাঁধা হতে পারে না। দরিদ্রদের মধ্যেও প্রতিভা থাকে। তাই দরিদ্রকে সামান্য সাহায্য না করে তার ভিতরের প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করা উচিত। শিক্ষা হলো মানসিক পরিবর্তনের অন্যতম মাধ্যম। যা গাছের নিচে বসেও অর্জন করা যায়। টিকিয়ে রাখার জন্যই বৃত্তি দেয়া হয়। তাই সব বাধাকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।’ আবার, কৃষি নিয়ে দেশের সার্বিক চিত্রের কথা বলেছেন এভাবে, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে এই লাইনে রয়েছি। বিভিন্ন দেশে গিয়েছি। ইউএস, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ইন্ডিয়া, মরিশাস, আফ্রিকা, তানজানিয়া, মোজাম্বিক, এশিয়া, আফ্রিকাসহ অনেক দেশের এগ্রিকালচার দেখেছি। বাইরের দেশের তুলনায় আমাদের কৃষির অবস্থা অনেক ভালো হতে পারে। আমাদের ভূমি ভালো আছে। কৃষকেরাও অনেক কিছু জানেন। কৃষিতে অনেক উন্নতি হয়েছে। আমি যে শুধু নেগেটিভ কথা বলব, তা নয়। কিন্তু আরও ভালো হতে পারে। আমাদের কৃষকদের অবস্থা তো ভালো না। সেটিই হচ্ছে সমস্যা। গরিব মানুষ দিয়ে আর কতই বা ভালো করানো যায়।’
ড. আবেদ চৌধুরী কবিতাসহ নানা বিষয়ে বই লিখেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও নানা বিষয়েও বিশেষ প্রবন্ধ লিখে থাকেন। তেমনি একটি বিশেষ রচনা ‘নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে শোধ হবে বাংলা ভাষার ঋণ’ শিরোনামে আবেদ চৌধুরী (৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬) লিখছেন,‘বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান জানাবার সবচেয়ে বড় উপায় হলো- এই ভাষায় নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা অথবা উচ্চাঙ্গ অনুবাদের মাধ্যমে এই ভাষাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষায় পরিণত করা। দুটোই কঠিন কাজ। কিন্তু এই কাজটুকু আমাদের করতেই হবে। আমি এই কাজে আমার সাধ্যমত ব্রতী হয়েছি। ভিডিওর মাধ্যমে জেনেটিকস, আধুনিক জীববিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়কে বাংলায় ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমার বিজ্ঞানের কাজ বাংলায় লিখছি। জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও মৌলিক বিজ্ঞান- দুটোর চর্চাই বাংলায় করছি ও করবো। এভাবে আমার ক্ষুদ্র কাজের মাধ্যমে আমি ঋণ শোধ করতে চাই তাদের যারা ১৯৫২ তে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। আরেকটা জরুরি কাজ হলো- আমাদের সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের কাজকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা। এই কাজটাও করতে হবে পরিশ্রমের সাথে। এজন্য চাই এমন মানুষ যাদের দুই ভাষাতেই সমান দখল রয়েছে। এমন মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আমি বাংলা কবিতা অনুবাদের কাজ শুরু করেছি। একটা বইও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। আরো কাজ আগামিতে করার ইচ্ছা রাখি। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এই দুই কাজের জন্য অনুকূল নয়। আমাদের ছাত্রদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে। অপরদিকে শিক্ষার ব্যাপ্তিও বাড়াতে হবে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার মান দিন দিন কমছে। অনুবাদের কাজে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও এগিয়ে আসতে পারেন। ইংরেজির মাধ্যমে আমরা আমাদের আবহমান ভাষা ও সংস্কৃতির কথা তুলে ধরবো এই বিশ্বায়নের যুগে। এভাবেই আমরা আমাদের বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সুযোগ পাবো।’
‘বইপড়া ও আমার প্রান্তিক জীবন’ রচনায় আবেদ চৌধুরী (৮ নভেম্বর ২০১৩) লিখেছেন, ‘শিকড় মানেই তো এক প্রান্ত। তবু এই প্রান্তিক শিকড়ই জীবনকে খোরাক জোগায় ও সমৃদ্ধ করে।…আমি অতিক্ষুদ্র একজন। কিন্তু বিশাল কিছুটা হলেও বোধকরি ক্ষুদ্রকে বদলে দিতে পারে। বিশালের সম্মুখীন হলে ক্ষুদ্রের মধ্যে জাগে বিশাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। আর এই আকাঙ্ক্ষারও শক্তি অনেক। আমি পরবর্তী বছরগুলো লাইনাস পলিংয়ের কথা মনে রাখার চেষ্টা করেছি ও তাঁর বালক বয়সের সীমাহীন উৎসাহের কথা মনে রেখে কিঞ্চিত হলেও উদ্যমী হওয়ার চেষ্টা করেছি।’
মৌলভীবাজারের কৃতি সন্তান,অনন্য বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরীর জন্মদিনে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি। আবারো তাঁকে জানাই জন্মদিনের নিরন্তর শুভেচ্ছাঞ্জলি।
(তথ্যসূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক সমকালসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট)
লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভাসানটেক সরকারী কলেজ, ঢাকা।
আমার বার্তা/এমই